লিখেছেন আহমাদ ইশতিয়াক
ইন্টারমিডিয়েটে ভালো ফলাফল করেই অনার্সে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিত বিভাগে।
একদিন কলেজের ক্যান্টিনে বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর ভীষণ তর্ক হলো। তর্কের বিষয় কোন এক বন্ধুর লেখা পত্রিকাতে ছাপায়নি। বন্ধুর দাবী 'এখন নামকরা কেউকাটা না হলে তার লেখা পত্রিকাওয়ালারা ছাপায় না।' বেশীরভাগ বন্ধুই সমর্থন করলো সেই বন্ধুকে।
বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ বললো, ‘আমিও পাঠিয়েছিলাম, পাত্তাই দিলোনা মাইরি! এরা সব এক গোয়ালের গরু!' শুনেই ক্ষেপে উঠলেন প্রবোধকুমার। বললেন, ‘তোরা যা বলছিস ওটা হতেই পারেনা। লেখা ভালো হয়নি বলেই ছাপায়নি। লেখা ভালো হলে অবশ্যই ছাপাতো।’ বন্ধুরা বললো, ‘ছাড় ছাড়, ওসব কল্পনা, কিন্তু এটাই বাস্তব।’ কিন্তু প্রবোধকুমারের তবুও আপত্তি। এক বন্ধু তখন পাল্টা জবাবে বললো, ‘তবে প্রমাণ করে দেখা। তুই একটা গল্প লিখে পাঠিয়ে দিয়ে দেখ তোর লেখা ছাপায় কিনা।’
বন্ধুদের সেই চ্যালেঞ্জ লুফে নিলেন প্রবোধকুমার। বললেন, আগামী তিন মাসের মধ্যেই গল্প লিখে নামী পত্রিকায় পাঠিয়ে প্রমাণ করবো।' সেই গল্প লিখতে গিয়ে থমকালেন প্রবোধকুমার। কারণ এই জীবনে কখনো গল্প তো লিখেনি সে। শেষমেশ তিন মাস তো দূরের কথা তিনদিনের মধ্যেই গল্প লেখা শেষ। গল্পের শেষে নিজের নামটা লিখতে গিয়ে থমকালেন প্রবোধকুমার। মা আদর করে তাঁকে ডাকতেন 'কালা মানিক' বলে। প্রবোধকুমার বদলে তাই মায়ের ডাকা ‘মানিক’ দিলেন জুড়িয়ে। অতঃপর সে গল্প নিয়ে সোজা হাজির হলেন বিচিত্রা পত্রিকার দপ্তরে।
বিচিত্রা পত্রিকার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সে সময় অফিসে ছিলেন না। তার জায়গায় বসেছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। স্মৃতিকথায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছিলেন, ‘একদিন বিচিত্রার দফতরে কালোপানা একটি লম্বা ছেলে এল। বলল গল্প এনেছি। বললাম, দিয়ে যান। সেই ছেলে লম্বা হাত বাড়িয়ে গল্পের পাণ্ডুলিপি দিয়ে বলল, এই যে রাখুন। এমন ভাব যেন এখুনি ছাপতে দিয়ে দিলে ভাল হয়। চোখে মুখে আত্মবিশ্বাস চুঁইয়ে পড়ছে। গল্প জমা দিয়ে সে চলে গেল। আমি তারপর এমনিই গল্পে একবার চোখ বোলাতে গিয়ে চমকে উঠলাম। এ যে রীতিমতো দুর্দান্ত গল্প!’
সেই গল্প ছাপা হলো, মানিক ভেবেছিলেন তার সেই গল্প কে পড়বে। কিন্তু সেই গল্পই লুফে নিয়েছিল পাঠকেরা। গল্প ছাপা হওয়ার পরে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে হাজির হয়েছিলেন মানিকের বাড়িতে। সঙ্গে গল্পের পারিশ্রমিক বাবদ ২০ টাকা। আবদার, ‘এখন থেকে আপনি আমাদের পত্রিকায় নিয়মিত গল্প লিখবেন।’
কলেজের ভর্তি হওয়ার বছরেই বাম রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়েছিলো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে গল্প ছাপা হওয়ার পরে শুরু হলো দিনরাত সাহিত্য চর্চা। কলেজের পড়াশোনা উঠলো লাটে। পরপর দু বছর অনার্সে ফেল করলেন। তখন তাঁর জন্য মাসে মাসে টাকা পাঠাতেন বড়দা। কিন্তু যখনই ভাইয়ের রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া আর সাহিত্য চর্চার খবর তার কানে পৌঁছালো তখন চিঠিতে ভাইকে লিখলেন, ‘তোমাকে ওখানে পড়াশোনা করতে পাঠানো হয়েছে। গল্প লিখতে আর রাজনীতি করতে নয়! ফেল করেছো কেন জবাব দাও?’
উত্তরে মানিক লিখেছিলেন, ‘গল্প উপন্যাস পড়া, লেখা এবং রাজনীতি ছেড়ে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’
চিঠি দেখেই রাগে ফুঁসতে লাগলেন বড়দা। ফিরতি চিঠিতে বড়দার জবাব ছিল এমন, ‘তোমার সাহিত্য চর্চার জন্য খরচ পাঠানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি টাকা দিতে পারবো না। নিজেরটা এবার নিজেই দেখো!’
প্রতিউত্তরে মানিক যা লিখেছিলেন তা আজকের সময় ভাবলে কি অবিশ্বাস্যই না লাগে মানিক লিখেছিলেন ‘আপনি দেখে নেবেন, কালে কালে লেখার মাধ্যমেই আমি বাংলার লেখকদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে স্থান করে নেব। রবীন্দ্রনাথ- শরৎচন্দ্রের সমপর্যায়ে ঘোষিত হবে আমার নাম। অথচ বয়স তখন তাঁর মাত্র ১৭।
মা হারানো মানিক দাদার অর্থ বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও বাদ দেননি সাহিত্য। কারণ সাহিত্য ততোক্ষণে তাঁকে পুরোপুরি গ্রাস করে নিয়েছে। একসময় কলেজের হোস্টেল ছেড়ে উঠলেন আমহার্স্ট স্ট্রিটের একটি মেসে। দিনরাত এক করে নাওয়া খাওয়া ভুলে তখন মানিক শুধু লিখেই গেলেন। ভুলে গেলেন নিজের শরীরের কথা। দ্বারে দ্বারে ঘুরলেন প্রকাশকদের।
পদ্মা নদীর মাঝি ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় উপন্যাস। ‘পদ্মা নদী মাঝি’ কীভাবে লিখেছিলেন মানিক সেটিও এক বিশাল কাহিনী। সংক্ষেপেই বলি, সালটা ত্রিশের দশকের শুরুর দিকের। তখন বাবার চাকরির সুবাদে টাঙ্গাইলে থাকতেন মানিকরা। বাঁশি তখন তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। মাঝেমাঝেই বাঁশি হাতে বেরিয়ে পড়তেন একা একা। আদাড়েবাদাড়ে, নদীর ধারে ঘুরে বেড়ান মানিক সঙ্গে গান আর বাঁশি।
বাড়ি ফেরার হুঁশ থাকে না তার। ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান কিংবা নৌকোর মাঝিদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে আড্ডা। কখনো কখনো আড়ালে এক দু'দিন থেকেও যান তাঁদের সঙ্গে। তখন তাঁর বয়স ১৪ কিংবা ১৫। একদিন হঠাৎই নিখোঁজ হলেন বাড়ি থেকে। কয়েক দিন পেরিয়ে গেলেও তাঁর ফেরার নাম নেই। শেষমেশ তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল টাঙ্গাইলের এক জেলে পল্লীতে। সেখানে জেলে আর মাঝিদের সঙ্গে দিব্যি রয়েছেন মানিক। কে জানতো জেলে পল্লীর সেই স্মৃতিই পদ্মা নদীর মাঝি লেখার ক্ষেত্রে তাঁকে বড় কাজে দিবে!
মজার বিষয় হলো একই বছর ছাপা হয়েছিলো মানিকের আরেক বিখ্যাত উপন্যাস ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' কীভাবে লিখেছিলেন মানিক সেটিও আরেক গল্প।
১৯৩৩ সালে কলকাতায় এসেছিলো এক বিখ্যাত পুতুল নাচের দল। সেই কার্নিভালের নাচ দেখে এমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন মানিক, যে সেই পুতুলদের সঙ্গে মানুষের জীবনকে মিলিয়ে লিখতে শুরু করলেন ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’। সেই উপন্যাস লিখতে বসে নিজের কথাই যেন ভুলে গিয়েছিলেন মানিক। পরবর্তীতে মানিকের লেখা এক চিঠিতে পাওয়া যায় তার বিবরণ। চিঠিতে মানিক লিখেছিলেন, “প্রথমদিকে ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ প্রভৃতি কয়েকটা বই লিখতে মেতে গিয়ে যখন আমি নিজেও ভুলে গিয়েছিলাম যে আমার একটা শরীর আছে এবং আমার পরিবারের মানুষরাও নিষ্ঠুরভাবে উদাসীন হয়ে গিয়েছিলেন। তখন একদিন হঠাৎ আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। একমাস থেকে দু’তিনমাস অন্তর এটা ঘটতে থাকে। তখন আমার বয়স ২৮/২৯, ৪/৫ বছরের প্রাণান্তকর সাহিত্যসাধনা হয়ে গেছে।”
ততোদিনে মানিক আক্রান্ত হয়ে গেছেন মৃগীরোগে। শরীর ও আর তখন সায় দিচ্ছে না। তার মধ্যেই দাঁতে দাঁত চেপে চলছিলো তাঁর জীবন লড়াই। এর সঙ্গে পেয়ে বসলো মদপানের নেশা। অবস্থা ভীষণ গুরুতর। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তখন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। বিধানচন্দ্র রায় মানিককে পরামর্শ দিয়ে বললেন, বিয়ে করে ফেলো। বিয়ে করলেন, এরই মধ্যে সন্তানও হলো। তখন মানিক পরিবার নিয়ে ঠাসাঠাসি করে থাকেন বরানগরে গোপাললাল ঠাকুর স্ট্রিটে। প্রবল প্রতাপে চলছে তাঁর লেখালেখি। কিন্তু এতো লেখালেখি করেও যেন সংসার আর চলছে না। বাধ্য হলেন চাকরি নিতে। কিন্তু কিছু দিন পরেই সে চাকরিতে ইস্তফা।
আবার পুরোদমে লেখা শুরু, সঙ্গে দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই। সে দারিদ্র যে কী ভয়ংকর তা বোঝা যায় মানিকের ডায়েরির একটি পৃষ্ঠা পড়লে। স্ত্রী ডলি অর্থাৎ কমলা এক মৃত সন্তানপ্রসব করেছেন, আর মানিক ডায়েরিতে লিখছেন, ‘বাচ্চা মরে যাওয়ায় ডলি অখুশি নয়। অনেক হাঙ্গামা থেকে বেঁচেছে। বলল, বাঁচা গেছে বাবা, আমি হিসেব করেছি বাড়ি ফিরে মাসখানেক বিশ্রাম করে রাঁধুনি বিদায় দেব। অনেক খরচ বাঁচবে।’
সংসারের এমন অবস্থায় মানিক ঠিক করলেন যেভাবেই হোক চাকরির জোগাড় করতেই হবে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছে ‘বঙ্গশ্রী’ পত্রিকায় সাপ্তাহিক বিভাগের জন্য সহকারী সম্পাদক প্রয়োজন।’ মানিক আবেদনও করলেন।
এদিকে সেই পদের জন্য আবেদন করেছিলেন সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামীও। মানিক বিষয়টি জানতে পেরে নিজের আবেদনপত্রের শেষে সম্পাদককে লিখলেন এমনটাই, ‘আমি অবগত আছি শ্রীপরিমল গোস্বামী এই পদটির জন্য আবেদন করিবেন। আমার চেয়েও তাঁহার চাকুরির প্রয়োজন বেশি। মহাশয় যদি ইতিমধ্যে তাহার সম্পর্কে অনুকূল বিবেচনা করিয়া থাকেন, তবে অনুগ্রহপূর্বক আমার এই আবেদন প্রত্যাহার করা হইল বলিয়া ধরিয়া লইবেন।’
এতদাসত্ত্বেও মানিকেরই চাকরি হলো শেষমেশ। মাসিক বেতন ৮৫ টাকা। শর্ত তাঁর লেখা ‘অমৃতস্য পুত্রা’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে হবে। এজন্য তিনি আরো ১০ টাকা সমানি পাবেন। কিন্তু ক মাস বাদে সেই চাকরিও ছেড়ে দিলেন মানিক। অথচ অভাব তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাচ্ছে। তার মধ্যে তিনি লিখেই চলেছেন। বামপন্থী ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের আন্দোলনে যুক্ত হয়ে কখনও একাই প্রাণের মায়া ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন কলকাতার হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা রুখতে।
১৯৫০ সালে যখন কমিউনিস্টদের ওপর নেমে এল চূড়ান্ত সরকারি দমননীতি, তখন বহু পত্রপত্রিকায় মানিকের লেখা ছাপানো বন্ধ করে দেওয়া হল। শুরু হলো ভয়ংকর অবস্থা। মদ ছাড়ার জন্য বহুবার চেষ্টা করেও পারলেন না তিনি।
একপর্যায়ে অভাবের তাড়নায় বাধ্য হয়েই লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে দাদাকে কিছু টাকা পাঠানোর জন্য চিঠি লিখলেন। জবাবে তাঁর দাদা লিখেছিলেন, ‘আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়, আমি কাউকে টাকা ধার দিই না।’
এদিকে প্রবল অসুস্থতার দরুন ঘনঘন অজ্ঞান হয়ে যান মানিক। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে জানলেন লিভার পঁচে গেছে। সেসময় মানিকের অবস্থা কেমন ছিল তা জানা যায় একটি ঘটনায়।
একদিন ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় পুজো সংখ্যার লেখা দিতে যাওয়ার সময় রাস্তায় মানিকের সঙ্গে দেখা হল অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্যের। মানিকের ভেঙে যাওয়া শরীর, মলিন জামাকাপড় দেখে খুব খারাপ লাগল দেবীপদর। জোর করে সে দিন তিনি মানিককে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে। ক্লান্ত মানিককে খেতে দিলেন দেবীপদর মা। বহুদিন পর ভালোমন্দ কিছু খেতে পেয়েছিলেন মানিক।
একসময় যে মানিক সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন ‘আমি শুধু সাহিত্যিকই হব, সেই মানিকই তখন লিখলেন, ‘দেখো, দুটি ডাল-ভাতের সংস্থান না রেখে বাংলাদেশে কেউ যেন সাহিত্য করতে না যায়।’
এর কিছুদিন বাদেই শারীরিক অসুস্থতার দরুন ফের হাসপাতালে ভর্তি হলেন মানিক। জিদ করে একবার ছাড়লেন। ফের আবার তাকে জোর করে ভর্তি করানো হলো। এর মধ্যে ৯ মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি তাঁর। এমতাবস্থায় বাড়িওয়ালা ঠুকলো তার বিরুদ্ধে মামলা। মানিকের কয়েকজন বন্ধু মিলে মোটা টাকার বিনিময়ে আদালতে মামলার দিন পিছিয়ে দিতে পারলেন বটে কিন্তু জীবনের আদালতে রায় ঘোষণার দিন যে মানিকের দিকে এগিয়ে আসছিলো তা দেখেনি কেউ।
২ ডিসেম্বর, গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে অসুস্থতার খবর পেয়ে ছুটে এলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। মানিকের স্ত্রী কমলাকে দেখতে পেয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বললেন, ‘বৌদি এমন অবস্থা, আগে টেলিফোন করেননি কেন?’
জবাবে কমলা উত্তর দিলেন ‘তাতে ও যে পাঁচ আনা পয়সা লাগে ভাই। সেটুকুও তো নেই যে ঘরে!’
সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় মানিককে ভর্তি করা হল কলকাতার নীলরতন হাসপাতালে। পরদিন ৩ ডিসেম্বরেই জীবনের সব হিসেব নিকেশ না চুকিয়েই চির ঘুমের দেশে হারিয়ে গেলেন মানিক।
মানিকের শেষযাত্রা নিয়ে সাহিত্যিক ও সাংবাদিক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন ‘পালঙ্ক শুদ্ধ ধরাধরি করে যখন ট্রাকে তোলা হয় তখন একটা চোখ খোলা, একটা বন্ধ। শরীরের ওপর রক্তপতাকা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ওপরে ফুল। মুখটুকু বাদে সমস্ত শরীরটা ফুলে আর ফুলে ছেয়ে গেছে। উপচে পড়ছে দুপাশে। মাথা এবং পায়ের কাছে দেশনেতা এবং সাহিত্যিক! সামনে পিছনে, দুইপাশে বহু মানুষ। সর্বস্তরের মানুষ। মোড়ে মোড়ে ভিড়। সিটি কলেজের সামনে মাথার অরণ্য। কিন্তু কাল কেউ ছিল না, কিছু ছিল না জীবনে এত ফুল তিনি পাননি কখনো।’
ঠিক যেন নিজের জীবনের স্বরূপ মানিক লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত প্রাগৈতিহাসিক গল্পের শেষভাগে। যেখানে লেখা ‘পথে দুদিকে ধানের ক্ষেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা। হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনোদিন পাইবেও না!’
আজ বেঁচে থাকলে মানিকের ১১৫ বছর পূর্ণ হতো। কিন্তু জীবন সংগ্রামে শ্রান্ত পথিক মানিক হারিয়ে গিয়েছিলেন মাত্র আটচল্লিশেই।
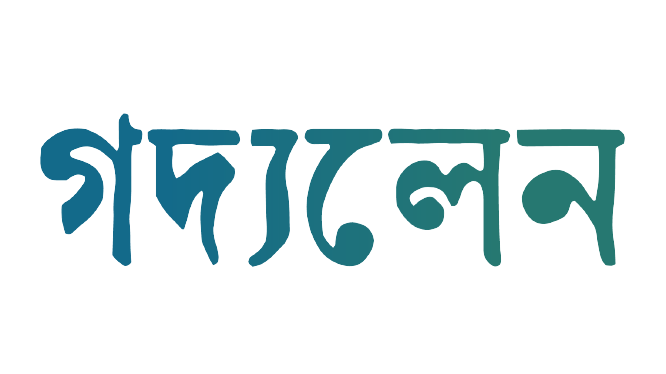







0 মন্তব্যসমূহ
প্রাসঙ্গিক ও মার্জিত মন্তব্য করুন